স্পর্শ
পৃথিবীর সব যুদ্ধই শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় মহান দর্শনে এসে। তা মহাভারতের কুরুক্ষেত্র হোক কিম্বা ট্রয় নগরীর ধ্বংস। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উঠে আসা গভীর উপলব্ধি মানুষকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে কোন না কোন দর্শনের আশ্রয়ে। যুদ্ধের বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি, হানাহানি, রক্তপাত সেই দর্শনের ছোঁয়ায় হয়ে উঠবে যেন কল্পনার ভাসমান দৃশ্য। যুদ্ধ শেষের বিস্তীর্ণ রণভূমি ভরে উঠবে কনে দেখা আলোয়। পরিত্যক্ত তরবারি, সহস্র ঘোড়ার ছুটে যাওয়ার আওয়াজ, দিগন্তে ধুলোর ঝড় সবকিছু হয়ে উঠবে মায়াবী, মোহময়ী। সমস্ত ধবংসলীলা তখন এক হয়ে গেয়ে উঠবে জীবনেরই জয়গান।
শুধু যুদ্ধ নয়, জীবনযুদ্ধের গল্পও অনেকটা একই।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পলি পড়ে। বর্তমানের কঠিন কর্কশভাব হয়ে ওঠে অতীতের ঘোরলাগা স্মৃতি। এক এক দৃশ্য চোখের সামনে জড়ো হয়, ফুটিয়ে তোলে যেন চলচ্চিত্রের কোন মন্তাজ।
আমি মফস্বলের মানুষ। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা দুটোই কলকাতা মহানগর থেকে পঁয়তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার দূরের ছোট্ট এক জনপদে।গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে। আমার শহর আয়তনে ছোট। কিন্তু ঐতিহ্যে সুবিশাল। বট অশ্বত্থের মতো দাঁড়িয়ে থাকা এই সুপ্রাচীন কলকাতা নগরীর থেকেও বয়সে বড়। সেকালের ব্রিটিশ ভারত থেকে তিনদিক পরিখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং সম্পূর্ণ এক দ্বীপ। এরকম একটি শহরের নিজস্বতা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। শহরতলির সেই নিজস্ব নিয়ম মেনেই বড় হয়ে উঠেছিলাম আমি। নির্দিষ্ট এক গণ্ডির মধ্যে অবাধ বিচরণ ছিল আমার। স্কুল কলেজ সবই বাড়ির কাছে। ট্রেন বাস চেপেও যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। বাহন বলতে একমাত্র সাইকেলই যথেষ্ট।
ছোট থেকেই আমার মধ্যে জাঁকজমকের হাতছানি কম। দিনভর ছুটে চলা নাগরিক ব্যস্ততা,রাতের মোহময়ী আলো কিম্বা সাহেবি কেতায় ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়া তরুণী, সে যাইহোক না কেন কোনদিনই সেভাবে টানেনি আমায়। তাই কলকাতা শহরও চেনা হয়ে ওঠেনি সেই ভাবে।বলা ভাল প্রয়োজন পড়েনি। পরিচয় ঘটেনি কলকাতার তিনশো বছর পুরোনো জটিল জটাজুটের সঙ্গে। ছোটবেলায় অনেকেই বাবা মা’র হাত ধরে বেড়াতে আসে – চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম আরও কত জায়গা। আমাদের অবস্থা সেরকম ছিল না। সামান্য দুটো টালির ঘর। বাবা মায়ের কাছে ওসব ছিল বিলাসিতা। একটু বড় হয়ে দু-চারবার বন্ধুদের সঙ্গে গেছিলাম বটে। তবে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।
কলকাতা শহর সেই কৈশোরের আমাকে দেখে মুচকি হেসেছিল নিশ্চয়। সংসারের অভিজ্ঞ অভিভাবক যেভাবে পরিবারের কিশোর ছেলেটার উদাসীনতায় হাসে। মনে মনে বলেছিল মনে হয়, না হে না, কটা বছর যাক, সেই আমারই শরণাপন্ন হতে হবে। লুটিয়ে পড়তে হবে আমার পায়ে।
হ্যাঁ, লুটিয়ে পড়েছিলাম কিনা জানি না। তবে কলেজ শেষের দু-এক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস লাখ লাখ সরকারি চাকুরিপ্রার্থীর মতো আমার কাছেও হয়ে উঠেছিল এক তীর্থক্ষেত্রের মতো।
আমাদের সময় সারা বছর ধরেই বেশ কিছু শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি বের করত কমিশন। যদিও তা সত্তর কিম্বা নব্বইয়ের দশকের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আমরা আবেদন করতাম। সেটা অনলাইন, ইন্টারনেটের যুগ নয়। ফুটপাথের খবরের কাগজ বিক্রেতা আর কিছু কিছু বইয়ের দোকান রাখত। সাধারণ কাগজে ছাপা ফর্ম। তার মধ্যেও ভাগাভাগি ছিল। সব পরীক্ষার ফর্ম সবাই রাখত না। আমাদের শহরে একটা দোকান ছিল যে শুধু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফর্ম বিক্রি করত। দাম দু-টাকা কিম্বা তিন। আমরা ওখানেই যেতাম। ওখানে সব পরীক্ষার ফর্ম পাওয়া যেত। দোকানের সাইনবোর্ড ছিল না, নাম জানতাম না। তবুও কোন মন্ত্রবলে প্রতি বছর কলেজ পাশ সমস্ত ছেলেরাই দলে দলে জেনে যেত এই দোকানের খবর। আমি খুব অবাক হতাম সেই দোকানির কথা ভেবে। পুরোনো একখানা ঘর। রঙচটা নোনাধরা দেওয়াল। ছাদের কড়ি বরগাগুলোরও অবস্থা খারাপ। ভেঙে পড়তে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ইলেকট্রিক নেই। সন্ধে হলে মোমবাতি জ্বালিয়ে চাকুরিপ্রার্থীর অপেক্ষা করত দোকানি। দোকানের হাল দেখে অনুমান করতে পারতাম তার সংসারের অবস্থা। আমার এক বন্ধু বলেছিল, রাজ্য সরকারি চাকরির অবস্থা এর চাইতে খুব ভালো কিছু নয় বিশেষত করণিক শ্রেণীর। কেন্দ্রীয় সরকার কিম্বা রেলওয়েজ-এর তুলনায় বেতন প্রায় এক তৃতীয়াংশ। তবুও কেন জানি না আমি সেই কেরানি হওয়ার আবেদনপ্ত্রই পূরণ করতাম বারবার। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ঘর বারান্দা জুড়ে পুরোনো ফাইল আর কাগজপত্রের গন্ধের কথা শুনেছি, শুনেছি বড় বড় সিলিং পাখাদের নেশা ধরানো একটানা ঘুরে যাওয়ার কথা, কিম্বা পড়ন্ত বিকেলে ফাঁকা ঘরজোড়া ধু ধু নিস্তব্ধতার মাঝে একলা কোন কেরানির মাথাগুঁজে কলম পিসে চলা। কেমন যেন ঘোর লাগত একটা। মনে হত জ্বরের মধ্যে আছি। চোখের সামনে আবছা ভেসে উঠত কল্পনার এক রাইটার্স বিল্ডিং। লালরঙ, ব্রিটিশের বুটের দাপট, বিনয় বাদল দিনেশের হঠাৎ ঢুকে পড়া। এরকম আরও কত কী!
সেই সময় আবেদনপত্র পূরণ করে পাঠাতে হত সাধারণ ডাকযোগে। আমরা পাঠাতাম না। বিশ্বাস করতাম ভবিষ্যতের ভার নিজেদের হাতে যতটা সুরক্ষিত ডাক বিভাগের কাছে ততটা নয়। কয়েকজন মিলে দল বেঁধে চলে যেতাম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিস,কলকাতা, মুদিয়ালি, হাতে হাতে জমা করতে। মুখবন্ধ বাদামি খাম, ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা নাম ঠিকানা, ফেলে আসতাম কমিশনের রাখা পাত্রে। লাখ লাখ আবেদনপত্রের মাঝে। সৌগত বলত, ওরে এটা পরীক্ষা নয়, স্বয়ম্বরসভা। কার গলায় যে মালা উঠবে! অভিরূপ বলত, মালা নিজে থেকে উঠবে না সোনা, অর্জুনের মতো মাছের চোখে তীর মেরে ছিনিয়ে আনতে হবে। আমরা হাসাহাসি করতাম অনাগত সেই দিনের কথা ভেবে। আমাদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ত নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভবিষ্যত জীবনের এক স্বপ্ন। রাস্তা পেরিয়ে আমরা চলে আসতাম উলটো ফুটে। একটা চায়ের দোকানে বসতাম। চা সিগারেট খেতাম।
সারা কলকাতা শহরের মধ্যে ওইটুকু জায়গাই হয়ে উঠেছিল আমার পরিচিত। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়েই উলটো দিকে গঙ্গার ধারে তখন ছিল মিনিবাস স্ট্যান্ড। গড়িয়া, নাকতলা, কালিতলা আরও কত মিনি। মুখস্থ হয়ে গেছিল সব নাম। কোনটায় কোনটায় উঠতে হবে আমায়। ওদিকে হাজরা পেরলেই কালীঘাট, রাসবিহারী। ট্রামলাইনটা ছিল আমার মার্কা। বাসের জানালা দিয়ে উঁকি মারতাম। ট্রামলাইন দেখা দিলেই ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে যেত নামার প্রস্তুতি।
সেদিন চৈত্রমাস। কিম্বা কে জানে বৈশাখও হতে পারে। কলকাতার রাস্তায় গরমের ঘোলাভাব। বাতাসের তীব্র ঝলসানি থেকে বাঁচতে পথচারীর সংখ্যা কম। কুকুরগুলোও সব গা ঢাকা দিয়েছে কে জানে কোথায়! উপায় নেই শুধু ট্রাফিক সার্জেন্টদের। রুমালে মুখ বেঁধে তারা ব্যস্ত কর্তব্য পালনে। মেইনসের পরীক্ষা ছিল। দশটা থেকে একটা। পাশ করলে ইন্টারভিউ। পরীক্ষাটা প্রত্যাশা মতো হয়নি। একাই ছিলাম। ধীর পায়ে গিয়ে বসেছিলাম সেই চায়ের দোকানে। তাকিয়েছিলাম রাস্তার দিকে। এবারেও হল না মনে হচ্ছে। নিজের মনেই মাথা নাড়ছিলাম ঘন ঘন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছিল চাপা দীর্ঘশ্বাস।
অপেক্ষা করছিলাম বাসের জন্য। হঠাৎ কানে এল এক মহিলাকণ্ঠ। হাওড়া যাওয়ার বাস এলে একটু হাত দেখাবেন তো! আমি তাকিয়ে দেখি মাঝবয়সি এক ভদ্রমহিলা। অন্ধ, হাতে লাঠি, চোখে চশমা। পরনের শাড়িতে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। বললাম, নিশ্চয়। আমিও তো হাওড়া যাব। একই সঙ্গে উঠে পড়া যাবে’খন। মহিলা ভদ্রতাসূচক হেসে বললেন, ও আচ্ছা! তারপর চুপ করে গেলাম দুজনেই। বাসে পাশাপাশি সিট। ভদ্রমহিলাই শুরু করলেন আবার। বাড়ি উত্তরপাড়া। হাওড়া থেকে মেইন লাইন ধরতে হয়। আমি বললাম, জানি। আমার বাড়িও ওই একই দিকে। উত্তরপাড়ার ওপর দিয়ে যেতে হয় আরও কয়েকটা স্টেশন। ভদ্রমহিলা গলায় আরও একটু স্নেহ মাখিয়ে বললেন, তাই নাকি! তাহলে তো খুবই ভালো। প্ল্যাটফর্ম অবধি যাওয়া যাবে একসঙ্গে। আমাকে লেডিসে উঠিয়ে দেবেন একটু। আমি বললাম, একদম চিন্তা করবেন না। কিন্তু আপনি গেছিলেন কোথায়! ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, মুদিয়ালির কাছেই ছোট্ট একটা ব্লাইন্ড স্কুলে চাকরি পেয়েছি কিছুদিন হল। ফিরতে দেরি হয়। আজ হাফছুটি নিয়েছি। ভাইঝিটার জন্মদিন। ছ’য়ে পড়ল এবার। পিসি বলতে অজ্ঞান। ফিরলেই সোজা এসে পড়ে কোলের মধ্যে। আসলে ছোট থেকে বড় করেছি তো। কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলার মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল অদ্ভুত এক সুখানুভূতিতে। পূর্ণতার এক পরিতৃপ্তিতে। ভাবছিলাম জীবন যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন মরুভূমির মতো ওয়েশিশ সেখানে থাকবেই। উনি জিজ্ঞেস করলেন, তা ভাইটি তুমি কোথায় গেছিলে! আমি বললাম, চাকরির পরীক্ষা দিতে দিদি। ভালো হয়নি। এবারেও পাবো না। বলে চুপ করে রইলাম খানিক।
এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল। একমনে হেঁটে যাচ্ছিলাম সেদিকে। লেডিসে ওঠার ঠিক আগে ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত রাখলেন আমার। হাত মুখ ছুঁলেন। একগাল হেসে বললেন, কে বলেছে হবে না! রেজাল্ট বের হলে দেখো ঠিক নাম থাকবে তোমার। তারপর কথা শেষ করে উঠে গেলেন ট্রেনে। আমি তাকিয়ে রইলাম শূন্য চোখে।
সেই চাকরিটা আমি পাইনি। পাওয়ার কথাও ছিল না। তবুও কেন জানি জীবনের কঠিন সময়ে দাঁড়ালে ওই ভদ্রমহিলার গলাই শুনতে পাই বারবার- কে বলেছে হবে না! রেজাল্ট বের হলে দেখো ঠিক নাম থাকবে তোমার। ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়েও তাঁরই হাতের স্পর্শ পাই কপাল মাথা চিবুকজুড়ে। নতুন করে আবার বুক বাঁধতে ইচ্ছে করে।
লেখাটি লেখকের ‘জলের খোঁজে ভেসে’ গদ্য সংকলন থেকে পুনর্মুদ্রিত

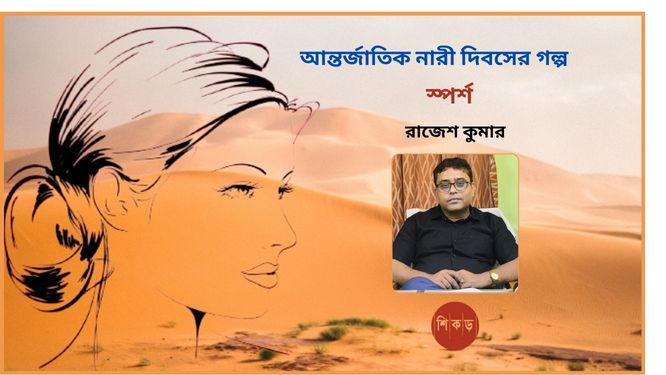




এখানে আপনার মন্তব্য রেখে যান